ব্যাংকগুলো এখন জমতে থাকা টাকা সরকারের বিভিন্ন বন্ড ও অন্যান্য ব্যাংকের বন্ডে বিনিয়োগ করে আমানতের খরচ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে সেখানেও চাহিদামতো বিনিয়োগ করতে পারছে না। ঋণের চাহিদা না থাকায় অনেক ব্যাংক ঋণের সুদহার কমিয়ে ৭ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। যদিও সুদের হার কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের সুদ সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। আবার অনেক ব্যাংক ঋণের সুদ কমানোর পাশাপাশি আমানতের সুদহারও কমিয়ে আড়াই শতাংশ করেছে। এতে সুদ আয়ের ওপর নির্ভরশীল আমানতকারীদের খরচ মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে। ব্যাংকগুলোও তারল্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কঠিন সময় পার করছে।
ব্যাংকাররা বলছেন, করোনার কারণেই ব্যাংক খাতে উপচে পড়া তারল্য পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অর্থনীতির গতি যে শ্লথ হয়ে পড়েছে, এটা তারই ইঙ্গিত। দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
জানতে চাইলে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আবুল কাশেম মো. শিরিন প্রথম আলোকে বলেন, সারা বিশ্বে চাহিদা না বাড়লে এই পরিস্থিতি ঠিক হবে না। চাহিদা বাড়লেই কেবল নতুন প্রকল্প হবে, নতুন ঋণ বিতরণ হবে। তখন আমানতের সুদও বাড়বে।
নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাংকগুলোকে গ্রাহকের গচ্ছিত আমানত থেকে ১৭ শতাংশ পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সিআরআর (নগদ জমা) ও এসএলআর (সংবিধিবদ্ধ জমা) হিসেবে রাখতে হয়। বাকি টাকা ঋণ দিতে পারে ব্যাংকগুলো। ইসলামি ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এই হার সাড়ে ৯ শতাংশ।
যমুনা ব্যাংকের এমডি মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ব্যাংকগুলো ভালো ও খারাপ গ্রাহকদের আলাদা ভাগে ভাগ করেছে। ভালো গ্রাহকদের ঋণের সুদ অনেক কমিয়েছে। আবার এসব গ্রাহক ধরতে অন্যান্য ব্যাংক সুদ আরও কমাচ্ছে। এ কারণে আমানতের সুদহার কমছে। তিনি বলেন, এখনো ঋণের চাহিদা আছে, তবে খারাপ গ্রাহকদের। তাই ব্যাংক এখনই ঋণ বাড়ানোর ঝুঁকি নিচ্ছে না। তবে এভাবে চলতে থাকলে একসময় এসব গ্রাহক ঠিকই ঋণ পেয়ে যাবেন।
মির্জা ইলিয়াস আরও বলেন, ব্যাংকে টাকা রয়েছে, তবে কেউ ফেলে রাখেনি। ১ শতাংশের কম সুদ পেলেও কোথাও না কোথাও রেখে দিয়েছে তারা।
ব্যাংকাররা বলছেন, এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনে কয়েকটি সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে। যেমন একদিকে প্রবাসী আয়ে উল্লম্ফন চলছে, অন্যদিকে আমদানি গতিহীন হয়ে পড়ছে। গ্রাহকদের মধ্যে খরচ কমে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ছে। নতুন প্রকল্প না থাকায় ঋণ বিতরণ সেভাবে বাড়ছে না। ব্যবসায়ীরা এখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বিদ্যমান ব্যবসাই ধরে রাখায় জোর দিয়েছেন। আবার অনেকেই প্রণোদনার ঋণ নিয়ে পুরোনো দায় শোধ করে চাপ কমানোর চেষ্টা করছেন।
সাধারণত ব্যাংকগুলোতে আসা প্রবাসী আয়ের অর্ধেক গ্রাহক তুলে নেন। বাকি অর্থ ব্যাংকগুলো আমদানি খাতে ব্যবহার করে। পাশাপাশি প্রতিটি ব্যাংকের ডলার রাখার একটি সীমা আছে। এর বেশি হলেই তা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বিক্রি করে দিতে হয়। করোনার কারণে আমদানি চাহিদা কম থাকায় বিদায়ী অর্থবছরে ব্যাংকগুলো থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ৭৯৪ কোটি ডলার কিনে নেয়। এর বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে ৬৭ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।
মার্চভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে পূবালী ব্যাংকে ৮ হাজার ৬০৮ কোটি টাকা, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকে ৭ হাজার ৭১৫ কোটি টাকা, যমুনা ব্যাংকে ৩ হাজার ১৬৭ কোটি টাকা, ব্যাংক এশিয়ায় ২ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা ও ইস্টার্ণ ব্যাংকে ২ হাজার ২১ কোটি টাকার অতিরিক্ত তারল্য ছিল।
ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের এমডি বলেন, ‘তারল্য ব্যবস্থাপনা এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই আমরা এসএমই ও রিটেইল ঋণে জোর দিয়েছি। এই ঋণের চাহিদা বাড়ছে। এরপর ভালো করপোরেট গ্রাহককে ঋণ দিচ্ছি। বাকি টাকা আমরা বিল-বন্ডে খাটাচ্ছি। তবে চাইলেও ইচ্ছেমতো বিল-বন্ড পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর আমরা অন্য ব্যাংককে টাকা ধার দিচ্ছি (প্লেসমেন্ট), না হলে কলমানিতে খাটাচ্ছি।’
সরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে গত মার্চ পর্যন্ত সোনালীতে ৪৩ হাজার ৮৫১ কোটি টাকা, অগ্রণীতে ২৩ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা ও জনতায় ১৩ হাজার ১০ কোটি টাকার অতিরিক্ত তারল্য ছিল। ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলোতেও ৩০ হাজার ১৭০ কোটি টাকা অতিরিক্ত তারল্য ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের (আইবিবিএল) কাছে। এর পেছনেই রয়েছে শাহজালাল ইসলামী ও আল-আরাফাহ্ ব্যাংক।
পূবালী ব্যাংকের এমডি শফিউল আলম খান চৌধুরী বলেন, ‘ব্যাংকে ভালো তারল্য আছে। তবে আমরা টাকা এমনিতেই ফেলে রাখছি না। সরকারের বন্ডে বিনিয়োগ করছি। অন্য ব্যাংকের বন্ডও কিনছি। আমানতের খরচ যাতে ওঠে, এই চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা।’ তিনি বলেন, বর্তমানে আমানতের সুদহার অনেক কম। এতে আমানতকারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ব্যাংকগুলোতে ঋণ প্রস্তাব আসছে। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলেই ঋণের চাহিদা বাড়বে।’

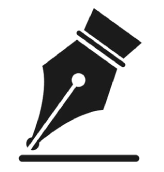


Discussion about this post